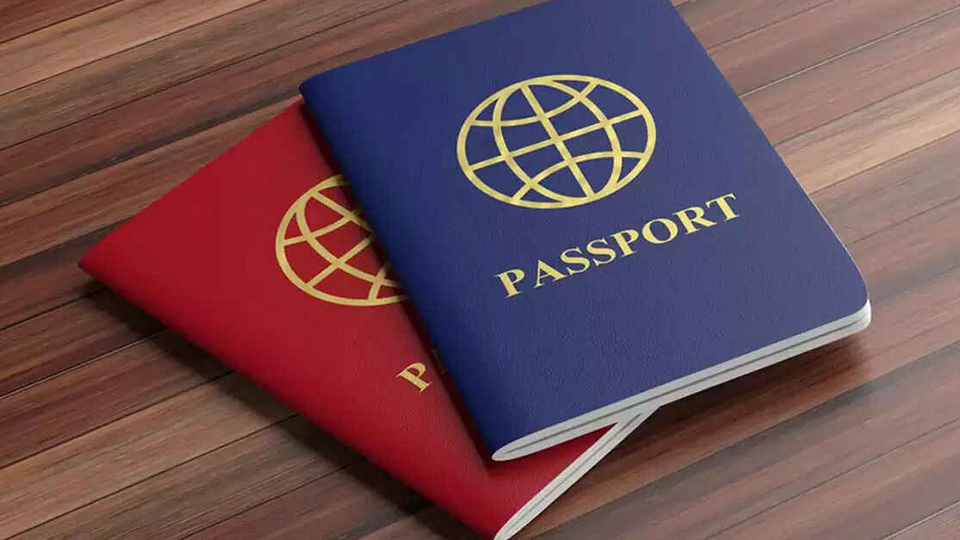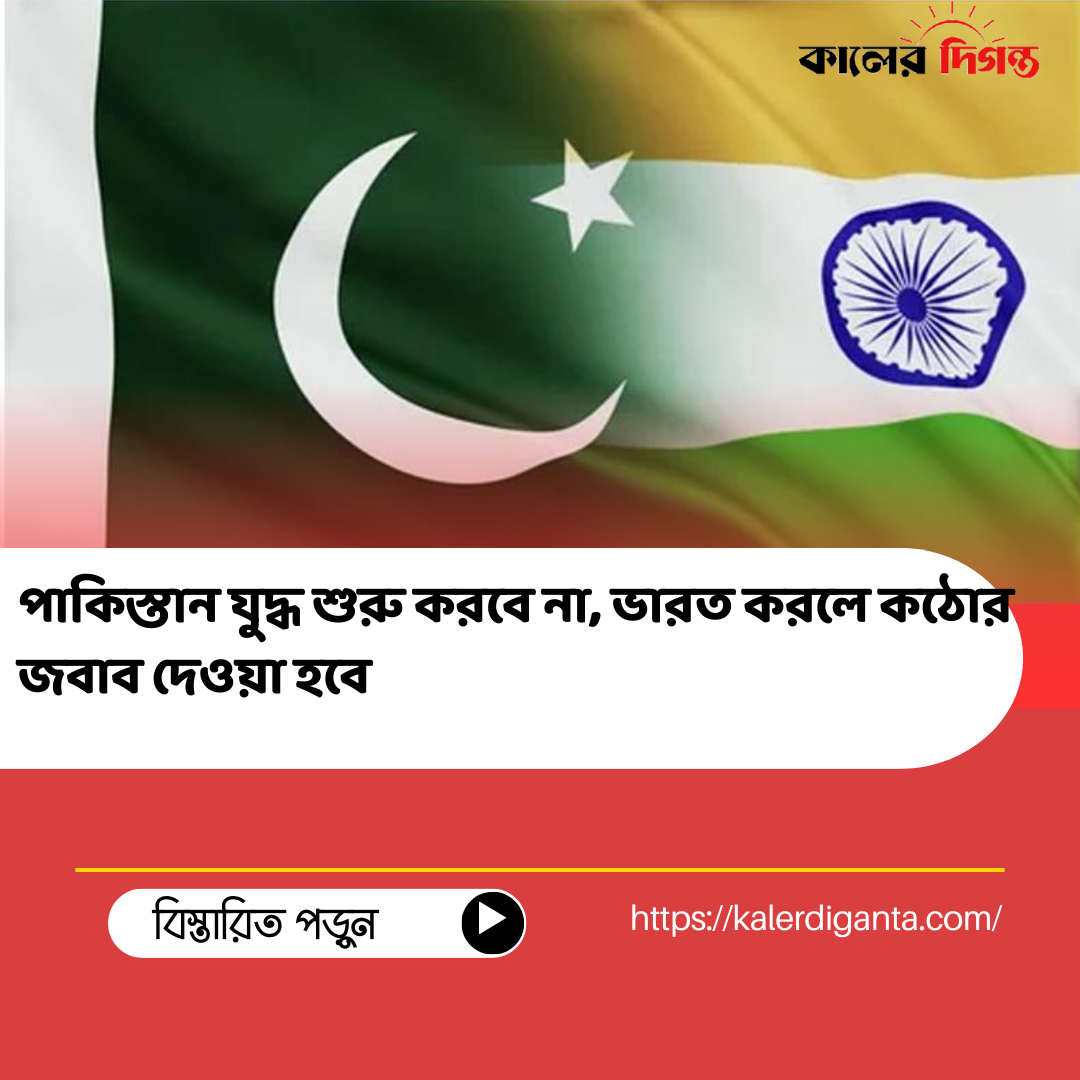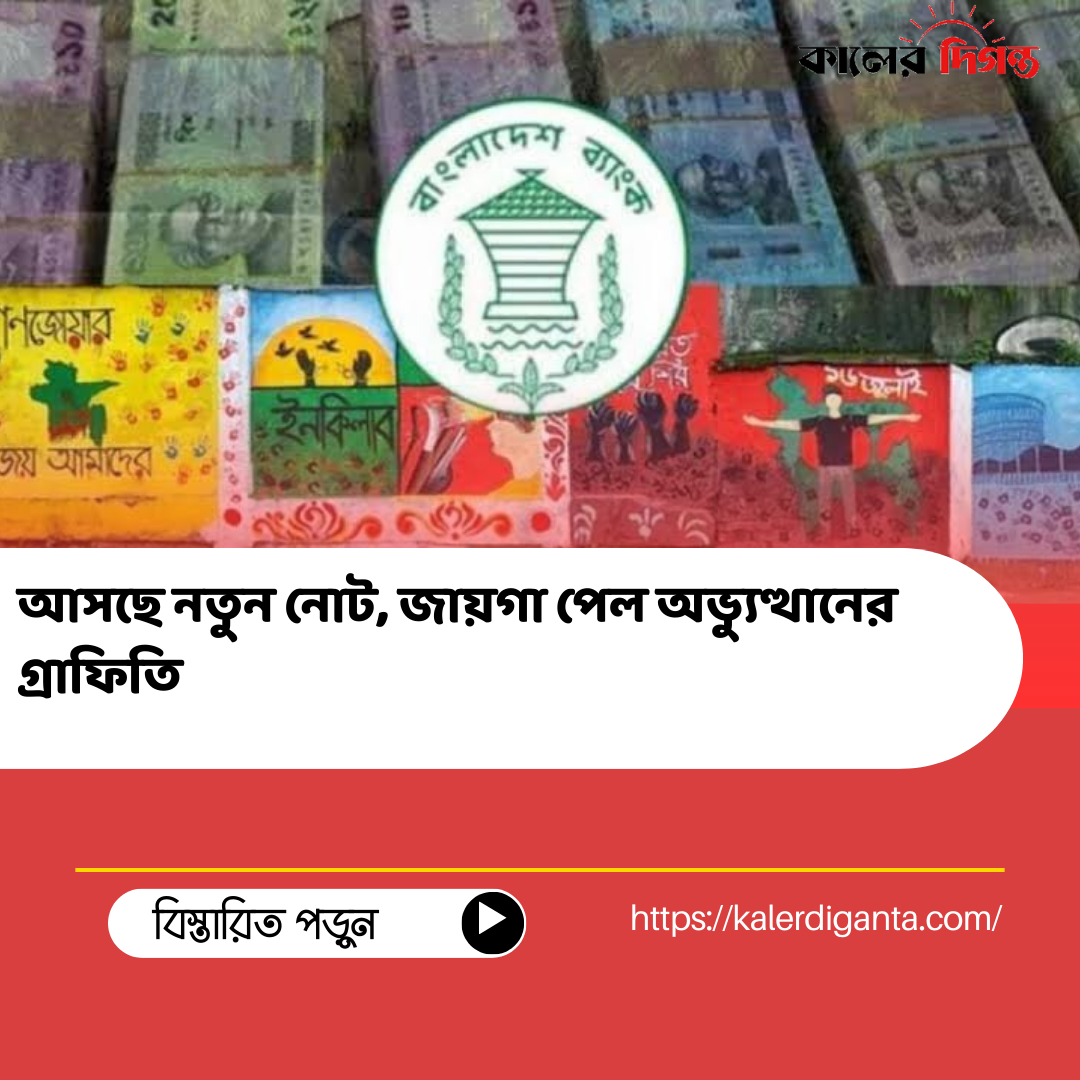বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিকভাবে তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত, যা ভূমিকম্পের জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করে। যদিও দেশটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল নয়, তবে সম্প্রতি কয়েকটি ছোট ভূকম্পন দেশটির ভূগর্ভে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আভাস দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে প্রতি বছর ১ মিটার থেকে দেড় মিটার সংকোচন হচ্ছে, যার ফলে ৮.২ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার শঙ্কা রয়েছে, যা যে কোনো সময় সংঘটিত হতে পারে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভূতত্ত্ব অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, “যদি এমন একটি বড় ভূমিকম্প হয়, তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঢাকা নগরী। অপরিকল্পিত শহর পরিকল্পনা এবং দুর্বল বিল্ডিং কোডের কারণে এক শতাংশও যদি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাৎক্ষণিকভাবে দুই লাখ মানুষ মারা যেতে পারে।” তিনি আরও জানান, ৫-৭ লাখ মানুষ ভবনগুলোর নিচে আটকা পড়তে পারে এবং পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব, অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য বিপর্যয়ের কারণে আরো মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে ভূমিকম্প সাধারণত এক থেকে দেড় হাজার বছর পর পর হয়, তবে ইতোমধ্যে গত বছর ৪১টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং ২০২৩ সালে তা বেড়ে ৫৪টি হয়েছে।
হাইকোর্টের নির্দেশে দেশে ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ১২ কোটি টাকার একটি নতুন প্রকল্পও চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স ও আর্মড ফোর্সেসের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।
তবে, অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, “ভূমিকম্পের আগে সচেতনতা এবং প্রস্তুতির বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার বর্তমানে ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধারকাজের প্রস্তুতিতে মনোযোগ দিচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।”
এছাড়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক নিতাই চন্দ্র দে জানান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বেশ কিছু অঞ্চলে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে, তবে ভূমিকম্পের প্রকৃত প্রস্তুতির জন্য এখনো বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্পের জন্য সরকারের প্রস্তুতি প্রয়োজন, বিশেষত ভূমিকম্পের আগে জনগণের প্রস্তুতি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।


 কালের দিগন্ত ডেস্ক :
কালের দিগন্ত ডেস্ক :